রাজবন্দীর জবানবন্দি
কাজী নজরুল ইসলাম
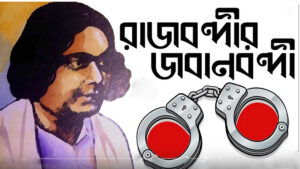
আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজবিদ্রোহী! তাই আমি রাজকারাগারে বন্দি এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত।
একধারে রাজার মুকুট; আরধারে ধূমকেতুর শিখা। একজন রাজা, হাতে রাজদণ্ড; আরজন সত্য, হাতে ন্যায়দণ্ড। রাজার পক্ষে রাজার নিযুক্ত রাজবেতনভোগী, রাজকর্মচারী। আমার পক্ষে – সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক, আদি অনন্তকাল ধরে সত্য – জাগ্রত ভগবান।
আমার বিচারককে কেহ নিযুক্ত করে নাই। এ মহাবিচারকের দৃষ্টিতে রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, সুখী-দুঃখী সকলে সমান। এঁর সিংহাসনে রাজার মুকুট আর ভিখারির একতারা পাশাপাশি স্থান পায়। এঁর আইন – ন্যায়, ধর্ম। সে আইন কোনো বিজেতা মানব কোনো বিজিত বিশিষ্ট জাতির জন্য তৈরি করে নাই। সে আইন বিশ্ব-মানবের সত্য-উপলব্ধি হতে সৃষ্ট; সে আইন সর্বজনীন সত্যের, সে আইন সার্বভৌমিক ভগবানের। রাজার পক্ষে – পরমাণু পরিমাণ খণ্ড-সৃষ্টি; আমার পক্ষে – আদি অন্তহীন অখণ্ড স্রষ্টা।
রাজার পেছনে ক্ষুদ্র, আমার পেছনে – রুদ্র। রাজার পক্ষে যিনি, তাঁর লক্ষ্য স্বার্থ, লাভ অর্থ; আমার পক্ষে যিনি, তাঁর লক্ষ্য সত্য, লাভ পরমানন্দ।
রাজার বাণী বুদ্বুদ্, আমার বাণী সীমাহারা সমুদ্র।
আমি কবি, অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তি দানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী। সে বাণী রাজবিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায়বিচারে সে বাণী ন্যায়-দ্রোহী নয়, সত্য-দ্রোহী নয়। সে বাণী রাজদ্বারে দণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে, ন্যায়ের দুয়ারে তাহা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অম্লান, অনির্বাণ, সত্য-স্বরূপ।
সত্য স্বয়ং প্রকাশ। তাহাকে কোনো রক্ত-আঁখি রাজদণ্ড নিরোধ করতে পারে না। আমি সেই চিরন্তন স্বয়ম্-প্রকাশের বীণা, যে বীণায় চির-সত্যের বাণী ধ্বনিত হয়েছিল। আমি ভগবানের হাতের বীণা। বীণা ভাঙলেও ভাঙতে পারে, কিন্তু ভগবানকে ভাঙবে কে? একথা ধ্রুব সত্য যে, সত্য আছে, ভগবান আছেন – চিরকাল ধরে আছে এবং চিরকাল ধরে থাকবে। যে আজ সত্যের বাণীকে রুদ্ধ করেছে, সত্যের বীণাকে মূক করতে চাচ্ছে, সে-ও তাঁরই এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সৃষ্ট অণু। তাঁরই ইঙ্গিতে-আভাসে, ইচ্ছায় সে আজ আছে, কাল হয়তো থাকবে না। নির্বোধ মানুষের অহংকারের আর অন্ত নাই; সে যাহার সৃষ্টি, তাহাকেই সে বন্দি করতে চায়, শাস্তি দিতে চায়। কিন্তু অহংকার একদিন চোখের জলে ডুববেই ডুববে।
যাক, আমি বলছিলাম, আমি সত্যপ্রকাশের যন্ত্র। সে যন্ত্রকে অপর কোনো নির্মম শক্তি অবরুদ্ধ করলেও করতে পারে, ধ্বংস করলেও করতে পারে; কিন্তু সে-যন্ত্র যিনি বাজান, সে-বীণায় যিনি রুদ্র-বাণী ফোটান, তাঁকে অবরুদ্ধ করবে কে? সে-বিধাতাকে বিনাশ করবে কে? আমি মরব, কিন্তু আমার বিধাতা অমর। আমি মরব, রাজাও মরবে, কেননা আমার মতন অনেক রাজবিদ্রোহী মরেছে, আবার এমনই অভিযোগ-আনয়নকারী বহু রাজাও মরেছে, কিন্তু কোনো কালে কোনো কারণেই সত্যের প্রকাশ নিরুদ্ধ হয়নি – তার বাণী মরেনি। সে আজও তেমনই করে নিজেকে প্রকাশ করেছে এবং চিরকাল ধরে করবে। আমার এই শাসন-নিরুদ্ধ বাণী আবার অন্যের কণ্ঠে ফুটে উঠবে। আমার হাতের বাঁশি কেড়ে নিলেই সে বাঁশির সুরের মৃত্যু হবে না; কেননা আমি আর এক বাঁশি নিয়ে বা তৈরী করে তাতে সেই সুর ফোটাতে পারি। সুর আমার বাঁশির নয়, সুর আমার মনে এবং আমার বাঁশি সৃষ্টির কৌশলে। অতএব দোষ বাঁশিরও নয় সুরেরও নয়; দোষ আমার, যে বাজায়; তেমনই যে বাণী আমার কণ্ঠ দিয়ে নির্গত হয়েছে, তার জন্য দায়ী আমি নই। দোষ আমারও নয়, আমার বাণীরও নয়; দোষ তাঁর – যিনি আমার কণ্ঠে তাঁর বাণী বাজান। সুতরাং রাজবিদ্রোহী আমিও নই; প্রধান রাজবিদ্রোহী সেই বাণী-বাদক ভগবান। তাঁকে শাস্তি দিবার মতো রাজশক্তি বা দ্বিতীয় ভগবান নাই। তাঁহাকে বন্দি করবার মতো পুলিশ বা কারাগার আজও সৃষ্টি হয় নাই।
রাজার নিযুক্ত রাজ-অনুবাদক রাজভাষায় সে-বাণীর শুধু ভাষাকে অনুবাদ করেছে, তাঁর প্রাণকে অনুবাদ করেনি। তাঁর সত্যকে অনুবাদ করতে পারেনি। তার অনুবাদে রাজানুগত্য ফুটে উঠেছে, কেননা, তার উদ্দেশ্য রাজাকে সন্তুষ্ট করা, আর আমার লেখায় ফুটে উঠেছে সত্য, তেজ আর প্রাণঙ কেননা আমার উদ্দেশ্য ভগবানকে পূজা করা; উৎপীড়িত আর্ত বিশ্ববাসীর পক্ষে আমি সত্য-বারি, ভগবানের আঁখিজল! আমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নাই, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি।
আমি জানি এবং দেখেছি – আজ এই আদালতে আসামির কাঠগড়ায় একা আমি দাঁড়িয়ে নেই, আমার পশ্চাতে স্বয়ং সত্যসুন্দর ভগবানও দাঁড়িয়ে। যুগে যুগে তিনি এমনই নীরবে তাঁর রাজবন্দি সত্য-সৈনিকের পশ্চাতে এসে দণ্ডায়মান হন। রাজ-নিযুক্ত বিচারক সত্য-বিচারক হতে পারে না। এমনই বিচার প্রহসন করে যেদিন খ্রিস্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হল, গান্ধিকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হল, সেদিনও ভগবান এমনই নীরবে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁহাদের পশ্চাতে। বিচারক কিন্তু তাঁকে দেখতে পায়নি, তার আর ভগবানের মধ্যে তখন সম্রাট দাঁড়িয়েছিলেন, সম্রাটের ভয়ে তার বিবেক, তার দৃষ্টি অন্ধ হয়ে গেছিল। নইলে সে তার এই বিচারাসনে ভয়ে বিস্ময়ে থরথর করে কেঁপে উঠত, নীল হয়ে যেত, তার বিচারাসন সমেত সে পুড়ে ছাই হয়ে যেত।
বিচারক জানে আমি যা বলেছি, যা লিখেছি তা ভগবানের চোখে অন্যায় নয়, ন্যায়ের এজলাসে মিথ্যা নয়। কিন্তু হয়তো সে শাস্তি দেবে, কেননা সে সত্যের নয়, সে রাজার। সে ন্যায়ের নয়, সে আইনের। সে স্বাধীন নয়, সে রাজভৃত্য। তবু জিজ্ঞাসা করছি, এই যে বিচারাসন – এ কার? রাজার না ধর্মের? এই যে বিচারক, এর বিচারের জবাবদিহি করতে হয় রাজাকে, না তার অন্তরের আসনে প্রতিষ্ঠিত বিবেককে, সত্যকে, ভগবানকে? এই বিচারককে কে পুরস্কৃত করে? – রাজা না ভগবান? অর্থ না আত্মপ্রসাদ?
শুনেছি, আমার বিচারক একজন কবি। শুনে আনন্দিত হয়েছি। বিদ্রোহী কবির বিচার বিচারক কবির নিকট। কিন্তু বেলাশেষের শেষ-খেয়া এ প্রবীণ বিচারককে হাতছানি দিচ্ছে, আর রক্ত-উষার নব-শঙ্খ আমার অনাগত বিপুলতাকে অভ্যর্থনা করছে; তাকে ডাকছে মরণ, আমায় ডাকছে জীবন; তাই আমাদের উভয়ের অস্ত-তারা আর উদয়-তারার মিলন হবে কিনা বলতে পারি না। না, আবার বাজে কথা বললাম।
আজ ভারত পরাধীন। তার অধিবাসীবৃন্দ দাস। এটা নির্জলা সত্য। কিন্তু দাসকে দাস বললে, অন্যায়কে অন্যায় বললে এ রাজত্বে তা হবে রাজদ্রোহ। এ তো ন্যায়ের শাসন হতে পারে না, এই যে জোর করে সত্যকে মিথ্যা, অন্যায়কে ন্যায়, দিনকে রাত বলানো – এ কি সত্য সহ্য করতে পারে? এ শাসন কি চিরস্থায়ী হতে পারে? এতদিন হয়েছিল, হয়তো সত্য উদাসীন ছিল বলে। কিন্তু আজ সত্য জেগেছে, তা চক্ষুষ্মান জাগ্রত-আত্মা মাত্রই বিশেষরূপে জানতে পেরেছে। এই অন্যায় শাসন-ক্লিষ্ট বন্দি সত্যের পীড়িত ক্রন্দন আমার কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল বলেই কি আমি রাজদ্রোহী? এ ক্রন্দন কি একা আমার? না – এ আমার কণ্ঠে ওই উৎপীড়িত নিখিল-নীরব ক্রন্দসীর সম্মিলিত সরব প্রকাশ? আমি জানি, আমার কণ্ঠের ওই প্রলয়-হুংকার একা আমার নয়, সে যে নিখিল আর্তপীড়িত আত্মার যন্ত্রণা-চিৎকার। আমায় ভয় দেখিয়ে মেরে এ ক্রন্দন থামানো যাবে না! হঠাৎ কখন আমার কণ্ঠের এই হারা-বাণীই তাদের আরেক জনের কণ্ঠে গর্জন করে উঠবে।
আজ ভারত পরাধীন না হয়ে যদি ইংলন্ডই ভারতের অধীন হত এবং নিরস্ত্রীকৃত উৎপীড়িত ইংলন্ড-অধিবাসীবৃন্দ স্বীয় জন্মভূমি উদ্ধার করবার জন্য বর্তমান ভারতবাসীর মতো অধীর হয়ে উঠত, আর ঠিক সেই সময় আমি হতুম এমনই বিচারক এবং আমার মতোই রাজদ্রোহ-অপরাধে ধৃত হয়ে এই বিচারক আমার সম্মুখে বিচারার্থ নীত হতেন, তাহলে সেই সময় এই বিচারক আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যা বলতেন, আমি তো তাই এবং তেমনি করেই বলছি!
আমি পরম আত্মবিশ্বাসী! তাই যা অন্যায় বলে বুঝেছি, তাকে অন্যায় বলেছি, অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি, – কাহারও তোষামোদ করি নাই, প্রশংসার এবং প্রসাদের লোভে কাহারও পিছনে পোঁ ধরি নাই, – আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই – সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য-তরবারির তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, – তার জন্য ঘরের-বাইরের বিদ্রুপ, অপমান, লাঞ্ছনা, আঘাত আমার উপর পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষিত হয়েছে, কিন্তু কোনো কিছুর ভয়েই নিজের সত্যকে, আপন ভগবানকে হীন করি নাই, লাভ-লোভের বশবর্তী হয়ে আত্ম-উপলব্ধিকে বিক্রয় করি নাই, নিজের সাধনালব্ধ বিপুল আত্মপ্রসাদকে খাটো করি নাই, কেননা আমি যে ভগবানের প্রিয়, সত্যের হাতের বীণা; আমি যে কবি, আমার আত্মা যে সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা। আমি অজানা অসীম পূর্ণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। এ আমার অহংকার নয়, আত্ম-উপলব্ধির আত্মবিশ্বাসের চেতনালব্ধ সহজ সত্যের সরল স্বীকারোক্তি। আমি অন্ধ-বিশ্বাসে, লাভের লোভে, রাজভয় বা লোকভয়ে মিথ্যাকে স্বীকার করতে পারি না, অত্যাচারকে মেনে নিতে পারি না। তাহলে যে আমার দেবতা আমায় ত্যাগ করে যাবে। আমার এই দেহ-মন্দির জাগ্রত দেবতার আসন বলেই তো লোকে এ-মন্দিরকে পূজা করে, শ্রদ্ধা দেখায়, কিন্তু দেবতা বিদায় নিলে এ শূন্য মন্দিরের আর থাকবে কি? একে শুধাবে কে? তাই আমার কণ্ঠে কাল-ভৈরবের প্রলয়তূর্য বেজে উঠেছিল, আমার হাতে ধূমকেতুর অগ্নি-নিশান দুলে উঠেছিল, সে সর্বনাশা নিশানপুচ্ছে মন্দিরের দেবতা নট-নারায়ণ-রূপ ধরে ধ্বংস-নাচন নেচেছিলেন। এ ধ্বংস-নৃত্য নব সৃষ্টির পূর্ব-সূচনা। তাই আমি নির্মম নির্ভীক উন্নত শিরে সে নিশান ধরেছিলাম, তাঁর তূর্য বাজিয়েছিলাম। অনাগত অবশ্যম্ভাবী মহারুদ্রের তীব্র আহ্বান আমি শুনেছিলাম, তাঁর রক্ত-আঁখির হুকুম আমি ইঙ্গিতে বুঝেছিলাম। আমি তখনই বুঝেছিলাম, আমি সত্য রক্ষার, ন্যায়-উদ্ধারের বিশ্ব-প্রলয় বাহিনীর লাল সৈনিক। বাংলার শ্যাম শ্মশানের মায়ানিদ্রিত ভূমিতে আমায় তিনি পাঠিয়েছিলেন অগ্রদূত তূর্যবাদক করে। আমি সামান্য সৈনিক, যতটুকু ক্ষমতা ছিল তা দিয়ে তাঁর আদেশ পালন করেছি। তিনি জানতেন, প্রথম আঘাত আমার বুকেই বাজবে, তাই আমি একবার প্রলয় ঘোষণার সর্বপ্রথম আঘাতপ্রাপ্ত সৈনিক মনে করে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেছি! কারাগার-মুক্ত হয়ে আমি আবার যখন আঘাত-চিহ্নিত বুকে, লাঞ্ছনা-রক্ত ললাটে, তাঁর মরণ-বাঁচা চরণমূলে গিয়ে লুটিয়ে পড়ব, তখন তাঁর সকরুণ প্রসাদ চাওয়ার মৃত্যুঞ্জয় সঞ্জীবনী আমায় শ্রান্ত, আমায় সঞ্জীবিত, অনুপ্রাণিত করে তুলবে। সেদিন নতুন আদেশ মাথায় করে নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ আমি, আবার তাঁর তরবারি-ছায়াতলে গিয়ে দণ্ডায়মান হব। সেই আজও-না-আসা রক্ত-উষার আশা, আনন্দ, আমার কারাবাসকে – অমৃতের পুত্র আমি, হাসি-গানের কলোচ্ছ্বাসে স্বর্গ করে তুলবে। চিরশিশু প্রাণের উচ্ছল আনন্দের পরশমণি দিয়ে নির্যাতিত লোহাকে মণিকাঞ্চনে পরিণত করবার শক্তি ভগবান আমায় না চাইতেই দিয়েছেন! আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই; কেননা ভগবান আমার সাথে আছেন। আমার অসমাপ্ত কর্তব্য অন্যের দ্বারা সমাপ্ত হবে। সত্যের প্রকাশ-ক্রিয়া নিরুদ্ধ হবে না। আমার হাতের ধূমকেতু এবার ভগবানের হাতের অগ্নি-মশাল হয়ে অন্যায়-অত্যাচারকে দগ্ধ করবে। আমার বহ্নি-এরোপ্লেনের সারথি হবে এবার স্বয়ং রুদ্র ভগবান। অতএব, মাভৈঃ! ভয় নাই।
কারাগারে আমার বন্দিনী মায়ের আঁধার-শান্ত কোল ও অকৃতী পুত্রকে ডাক দিয়েছে, পরাধীনা অনাথিনি জননীর বুকে এ হতভাগ্যের স্থান হবে কিনা জানি না, যদি হয় বিচারককে অশ্রু-সিক্ত ধন্যবাদ দিব। আবার বলছি, আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই। আমি ‘অমৃতস্য পুত্রঃ’। আমি জানি –
ওই অত্যাচারীর সত্য পীড়ন
আছে, তার আছে ক্ষয়;
সেই সত্য আমার ভাগ্য-বিধাতা
যার হাতে শুধু রয়।
প্রেসিডেন্সি জেল, কলিকাতা
৭ জানুয়ারি, ১৯২৩।
রবিবার – দুপুর
নজরুল সৃষ্টিকর্তাকে নিজের বিচারক হিসেবে ধরেছেন। জবানবন্দিতে সৃষ্টিকর্তার প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ভারতের স্বাধীনতার জন্য আকুতি ফুটে উঠেছে।[৩]
নানা সঙ্কটের জালে আচ্ছন্ন ছিল নজরুলের সমাজব্যবস্থা। পুরো ভারতবাসী ছিল পরাধীনতার শৃঙ্খলে। পৃথিবীর চালচিত্র ছিল অমানবিক। বিভিন্ন যুদ্ধবিগ্রহ, শাসন-শোষণ, গ্লানি, বঞ্চনা, অন্যায়, অনিয়ম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর পোড়ামাটি নজরুলের হৃদয়কে করেছে অশ্রুসিক্ত। ১৯০ বছরের ঔপনিবেশিকদের করাল গ্রাসে নিমজ্জিত ভারতবাসীর নিজস্বতা স্বজাত্যবোধ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও মৌলিক অধিকারগুলো অস্তিত্বের সঙ্কটে পড়ে।
বিংশ শতকের শুরু থেকে যখন হতাশা, নিরাশা, দূরাশায় ঝাপসা অন্ধকার পুরো পৃথিবীকে ঝাপটে মেরে ধরে, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, মূল্যেবোধের অবক্ষয়, ভারতবাসীর কাঁধে উড়ে এসে জুড়ে বসে, ঠিক সেই মুহূর্তে বিষের বাঁশিতে অগ্নিবীণা বাজিয়ে ধূমকেতুর ন্যায় সত্যবাণী নিয়ে বিদ্রোহী নজরুলের, মানবতাবাদী নজরুলের, বিপ্লবী নজরুলের, প্রেমিক নজরুলের পদার্পণ। আসলে নজরুলের চেতনায় ও প্রেরণায় ছিল বন্ধুর মর্যাদার চেয়ে সত্যের মর্যাদা অনেক বড়।
সাহিত্যাকাশে এক বিস্ময় নক্ষত্র হিসেবে তার সফল বিচরণ। গান, কবিতা, প্রবন্ধ, গল্পগ্রন্থ, প্রবন্ধগ্রন্থ, উপন্যাস, নাটক, জীবনীগ্রন্থ, অনুবাদ, গীতসঙ্কলন, পত্রিকা সম্পাদনা হরেক সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইতিহাসে যেমন অমৃত লোক হিসেবে শতাব্দীর পর শতাব্দীর জন্য নিজের আসনকে পাকাপোক্ত করেছেন, তদরূপ পাঠকের মনের মুকুরে নিজেকে শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে আপন গুণে প্রশংসার পঞ্চমুখে পরিণত করেছেন। নজরুল তার মেধা, মনন, চিন্তাশীলতা, স্বদেশপ্রেম, উদার মানবিকতা, জাতিপ্রেমে নিজেকে সমাসীন করেছেন বৈশ্বিক নাগরিকে।
তার জীবন আন্দোলনে ছিল মুক্তিকামী মানবতার উচ্চারণধ্বনি। নজরুলের জন্ম পরাধীন দেশে বলেই আজীবন তিনি মুক্তিকামী মানবতার সপক্ষে তার লিখনী ধারণ করেছেন। ব্রিটিশ বেনিয়াদের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন খড়গহস্ত। যার ফলে নজরুল বিদ্রোহের অনন্য দ্যোতক তার অগ্নিবীণা। কাব্যগ্রন্থটি উন্মেষের সাথে সাথেই তার বিদ্রোহের প্রলয় ঝঞ্ঝায় ব্রিটিশ সিংহাসন টলমলিয়ে ওঠে। জুলুমবাজ জালিম সরকারের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহের কালজয়ী দৃষ্টান্ত বিদ্রোহী কবিতাÑ
‘মহা বিদ্রোহী রণকান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না’
ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম কবিতায় উচ্চারণ করেনÑ শংকারে করি লংকার পার কার ধনু টংকার।
আসলে ‘রাজবন্দীর জবানবন্দী’ প্রবন্ধে নজরুল আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যে জবানবন্দী দিয়েছেন, তাতে প্রমাণিত হয় সত্যিই তিনি শংকাকে লংকায় পার করেছেন। নজরুল ইসলাম সম্পাদিত ধূমকেতু পত্রিকার মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসন-শোষণ, অমানবিক, অনৈতিক, নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে নজরুলের বিদ্রোহ ভদ্রতার মাধ্যমে ুদ্রতা থেকে আর্দ্রতার দিকে ধাবিত হয়। নজরুল তার ধূমকেতুর মাধ্যমে সব অনিয়ম ও উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে সাধ্যমতো গদ্য লেখেন। তার লেখনীর প্রভাব ব্রিটিশের স্বভাবে আগুন ধরিয়ে দেয়। তার বক্তব্য পাঠকসমাজে হয় উজ্জীবিত। তার আগমন যেন মুক্তিকামী মানুষের বার্তাবাহক হিসেবে প্রভাব ফেলে।
অন্য দিকে তার অগ্নিবীণার আগুনে ব্রিটিশ মসনদ যেন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। বিদ্রোহের প্রলয় ঝঞ্ঝার দোদুল্যমান ব্রিটিশ সিংহাসনকে রক্ষায় তারা মরিয়া হয়ে ওঠে। অগ্নিবীণাকে কেন্দ্র করে (১৯২২ সালে) ব্রিটিশ বিচারক তাকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ১৯২৩ সালের ৭ জানুয়ারি মুক্তির জন্য যুক্তির উক্তি দিয়ে এক জ্বালাময়ী অভিভাষণ প্রদান করেন। সেই দীপ্তিময় উচ্চারণই পরিবর্তী সময়ে ‘রাজবন্দীর জবানবন্দী’ নামে সাহিত্যের রুপালি পাতায় সোনালি অধ্যায় হিসেবে স্থান করে নেয়।
নজরুল চাটুকার বিচারকের আদালতে ভয়-লেশহীন, ভীতি, সন্দেহ, সংশয় আশঙ্কা, মানবিক সব দুর্বলতাকে প্রবলতর উত্তাপ দিয়ে দলিত-মথিত করে ঐতিহাসিক ভাষণে ঘোষণা করেনÑ
আমি কবি অপ্রকাশক সত্যকে প্রকাশ করিবার জন্য অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তি দানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত।
তার মত দৃঢ়চেতা, প্রবল আত্মপ্রত্যয়ী, আত্মবিশ্বাসী সেকালে-একালে অথবা কস্মিনকালেও দৃশ্যমান হয়নি। আদালতকে তিনি বলেনÑ আমি পরম আত্মবিশ্বাসী। আর যা অন্যায় বলে বুঝেছি, অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি, কাহারো তোষামোদ করি নাই। প্রশংসা এবং প্রসাদের লোভেও কাহারো পিছনে পোঁ ধরি নাই।
আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই, সমাজের জাতির দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্যের তরবারির তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।
আমি অন্ধ বিশ্বাসে, লাভের লোভে, রাজভয়ে বা লোকভয়ে, মিথ্যাকে স্বীকার করতে পারি না। আমার হাতের ধূমকেতু আর ভগবানের হাতে অগ্নিমশাল হয়ে অন্যায়-অত্যাচারকে দগ্ধ করবে। আমার এই শাসনবিরুদ্ধ বাণী আবার অন্যের কণ্ঠে ফুটে উঠবে। নজরুল তার জবানবন্দীতে বলতে থাকেনÑ
‘আমার হাতের বাঁশি কেড়ে নিলেই সে বাঁশির মৃত্যু হবে না।’
কেননা আমি আর এক বাঁশি নিয়ে বা তৈরি করে তাতে সেই সুর ফোটাতে পারি। সুর আমার বাঁশির নয়, সুর আমার মনে এবং বাঁশির সৃষ্টির কৌশলে, অতএব দোষ বাঁশির নয়, সুরেরও নয়, দোষ তার, যিনি আমার কণ্ঠে তার বীণা বাজান, তিনি বলতে থাকেনÑ
সে বাণী রাজবিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে। কিন্তু ন্যায়বিচারে সে বাণী ন্যায়দ্রোহী নয়। সত্যদ্রোহী নয়। সে বাণী রাজদ্বারে দণ্ডিত হতে পারে। কিন্তু ধর্মের আলোকে ন্যায়ের দুয়ারে তা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অমøান, অনির্বাণ, সত্যস্বরূপ।
মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার ওপর অগাধ বিশ্বাস, আল্লাহর রাজত্বে, ক্ষমতায়, শক্তি সত্তায় তার অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস থেকে আদালতের কাঠগড়ায় দ্ব্যর্থহীন উচ্চারণ করেন তাকে শাস্তি দেয়ার মতো রাজশক্তি বা দ্বিতীয় ভগবান নেই। তাকে বন্দী করার মতো পুলিশ বা কারাগার আজো সৃষ্টি হয়নি।
নজরুল বিচারকের সীমাবদ্ধতা, তার ন্যায়বিচার করার এখতিয়ার কতটুকু আছে, বেশির ভাগ বিচারক সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে রায় দিতে ব্যর্থ হচ্ছেন, তাই বিচারককেই সামনে রেখে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করেনÑ বিচারক জানে আমি যা বলছি, যা লিখেছি, তা ভগবানের চোখে অন্যায় নয়, ন্যায়ের এজলাসে মিথ্যা নয়। কিন্তু হয়তো সে শাস্তি দেবে। কেননা সে সত্যের নয়, সে রাজার। সে ন্যায়ের নয়, সে আইনের। সে স্বাধীন নয়, সে রাজভৃত্য। তবু জিজ্ঞাসা করছি, এই বিচারাসন কার? রাজার না ধর্মের? এই যে বিচার, এ বিচারের জবাবদিহি করতে হয় রাজাকে, না তার অন্তরের আসনে প্রতিষ্ঠিত বিবেককে, সত্যকে? ভগবানকে? এ বিচারককে কে পুরস্কৃত করে? রাজা, না ভগবান? না আত্মপ্রসাদ?
নজরুল এটাও ব্যক্ত করেছেন, তার বিচারক একজন কবি, শাসক শ্রেণীর আঙুলের ইশারায় যে বিচার হবে তাতে বাধা দেয়ার মতো ক্ষমতাও বিচারক কবির নেই।
তাই সমগোত্রের হওয়া সত্ত্বেও নজরুল তার ওপর হতাশ হয়েছেন।
ব্যক্ত করেছেন হৃদয়ের উত্তাপ উচ্ছ্বাসগুলোÑ
শুনেছি আমার বিচারক একজন কবি। শুনে আনন্দিত হয়েছি। বিদ্রোহী কবির বিচার বিচারক কবির কাছে। কিন্তু বেলা শেষের শেষ খেয়া এ প্রবীণ বিচারককে হাতছানি দিচ্ছে, আর রক্ত-ঊষার, নব-শঙ্খ আমার অনাগত বিপুলতাকে অভ্যর্থনা করছে, তাকে ডাকছে মরণ, আমায় ডাকছে জীবন, তাই আমাদের উভয়ের অস্ত তারা আর উদয় তারার মিলন হবে কি না, বলতে পারি না। না! আবার বাজে কথা বললাম?
আজ ভারত পরাধীন। তার অধিবাসীবৃন্দ দাস। এটা নির্জলা সত্য। কিন্তু দাসকে দাস বললে, অন্যায়কে অন্যায় বললে এ রাজত্বে তা হবে রাজদ্রোহ। এত ন্যায়ের শাসন হতে পারে না, এই যে জোর করে সত্যকে মিথ্যা, অন্যায়কে ন্যায়, দিনকে রাত বলানো এটা কি সত্য সহ্য করতে পারে? এ শাসন কি চিরস্থায়ী হতে পারে? এত দিন হয়েছিল, হয়তো সত্য উদাসীন ছিল বলে। কিন্তু আজ সত্য জেগেছে, তা চুষ্মান জাগ্রত-আত্মা মাত্রই বিশেষ রূপে জানতে পেরেছে। এই অন্যায় শাসনকিষ্ট বন্দী সত্যের পীড়িত ক্রন্দন আমার কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল বলেই আমি রাজদ্রোহী? এ ক্রন্দন কি একা আমার? না এ আমার কণ্ঠে ওই উৎপীড়িত নিখিল নীরব ক্রন্দসীর সম্মিলিত সরব প্রকাশ? আমি জানি, আমার কণ্ঠের ওই প্রলয় হুঙ্কার একা আমার নয়, সে যে নিখিল আর্তপীড়িত আত্মার যন্ত্রণা চিৎকার। আমায় ভয় দেখিয়ে মেরে এ ক্রন্দন থামানো যাবে না। হঠাৎ কখন আমার কণ্ঠের এই হারা বাণীই তাদের আরেক জনের কণ্ঠে গর্জন করে উঠবে।
নজরুলের রাজবন্দীর জবানবন্দী সব রাজবন্দী, প্রতিহিংসার শিকার, অত্যাচারিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত, অপমানিত, নিগৃহীত চিত্তকে সাহস জোগাবে সত্যে উদ্ভাসিত হতে, অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে, পুতুল বিচারকের সম্মুখে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সত্যের অমিয় সুধাকে দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করতে।

